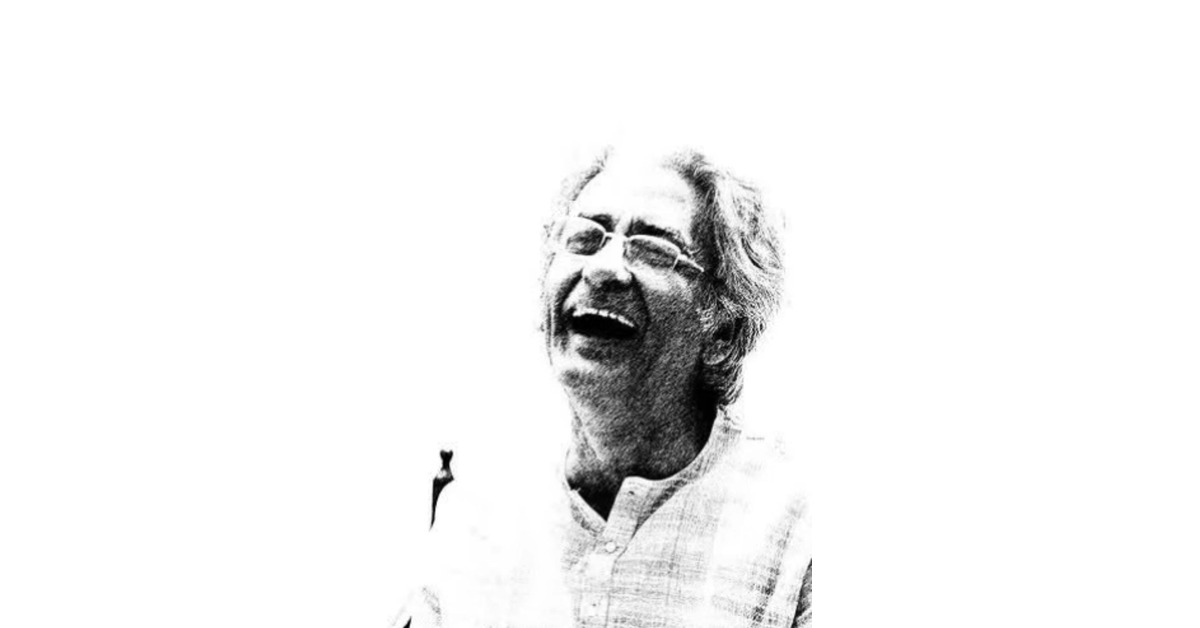প্রতুলদা চলে গেলেন। আমাদের পুরো একটা প্রজন্মের স্মৃতিবিস্মৃতির ঝিকিমিকি আলোয় তাঁর উদ্যত হাতের ভঙ্গি, তাঁর এলোমেলো চুল, মুখে শিশুসুলভ হাসি দপ্ করে জ্বলে উঠল, খবরটা পেয়েই। ‘ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে সাথীরে / ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে…’
পুরো উপমহাদেশে প্রতুলদার জুড়ি নেই, গানের ক্ষেত্রে, অন্তত একটা বিষয়ে। তিনি একই সঙ্গে বহু ক্ষেত্রেই গীতিকার, সুরকার, গায়ক এবং কণ্ঠই তাঁর বাদ্যযন্ত্র! গানের কথা এবং উপস্থাপনার অত্যাশ্চর্য সব কারুকাজ নিয়ে কথা বলার আগে, মনে রাখতে হবে, তিনি কী তন্ময় সাবলীলতায় সুরের সেতু নির্মাণ করতে পারতেন, এক কথা থেকে নতুন কথায়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে, সেই অবিস্মরণীয় গান—‘চ্যাপলিন’। তার লিরিকে ‘লাইমলাইট’ সিনেমার সেই তীব্র প্রেমের সংরাগ ‘লাভ লাভ লাভ লাভ…’ যাকে প্রতুল মুখোপাধ্যায় খোলা মাঠে বা প্রেক্ষাগৃহে জাগিয়ে তুলতেন ‘প্রেম প্রেম প্রেম…’। সেই গান শুনতে শুনতে মনে হত মানুষটি প্রায় অপার্থিব এক অনুভবে আমাদের সিঞ্চিত করে তুলছেন। আজকের ভারতবর্ষে সেই গানকে এত প্রাসঙ্গিকে মনে হয়! অপ্রেম আর ঘৃণার দম্ভে যখন প্রবল প্রতাপে ক্ষমতা শ্বাসরুদ্ধ করে রাখতে চাইছে আসমুদ্র হিমাচল, তখন প্রেম-ই হয়ে ওঠে দুর্বার, বেপরোয়া এক প্রতিরোধী আর তখনই প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরা আদ্যন্ত ‘রাজনৈতিক’ হয়ে ওঠেন। তাঁদের গানে এবং উপস্থাপনায় স্বৈরতন্ত্রের মোকাবিলা করার সাহস যেন চারিয়ে যায় জনমানসে।
আরও পড়ুন-অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ সম্ভব নয়
রাজনীতির সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই অবশ্য ছিল প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের। জন্মেছেন ১৯৪২ সালে। বরিশালে। স্বাধীনতা-উত্তর যুগের অগ্নিবর্ষী অনেক দশক স্বপ্ন লড়াই দেখেছেন। তৎসত্ত্বেও প্রথম গীতিসংকলন বেরোয় ১৯৮৮ সালে। মূলধারা তথা এসটাব্লিশমেন্টের সঙ্গে একটা আড়াআড়ি দূরত্ব রাখতে চাইত তাঁর গান। বামপন্থী তৃতীয় ধারার রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সখ্য হয়তো সেকারণেই এত দৃঢ়। কানোরিয়া এবং অন্যান্য জুট মিল আন্দোলনে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে তাঁর গান সংঘাতেই বেঁচেছে। আপোসে নয়। ‘হাত মিটিঙে চোঙা ফুঁকেছি, গেট মিটিঙে গলা ভেঙেছি / চিনছি শহর গ্রাম / স্লোগান দিতে গিয়েই আমি সবার সঙ্গে আমার দাবি / প্রকাশ্যে তুললাম…’। গানের অন্তর্বতী অংশকে এত সুরেলা, পর্দা বদলকে এত চমৎকার অনুরণনে ভরে দিতে তাঁর মতো কেউই পারেননি। কবীর সুমন তাঁকে বলেছিলেন ‘লোকটা আস্ত একটা গান’। ‘গণসংগীত’ যে কিছু জটিলতাহীন, রহস্যহীন, ‘একমাত্রিক’ ‘যান্ত্রিক’ বিবৃতি এবং রাজনৈতিক নির্দেশাবলি নয়। সেখানে শিল্পসাহিত্যের নানা বিমূর্ততার সঙ্গেও নিরন্তর সংলাপ চলে— প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গানের সামনে দাঁড়ালে সেকথা মনে পড়ত। বছর কুড়ি-বাইশ আগে বইমেলা থেকে বেরিয়েই দেখি খোলা আকাশের নীচে অনবদ্য ভঙ্গিমায় প্রতুলদা গাইছেন— ‘হেই ছোকরা চাঁদ / ও জোয়ান চাঁদ…’, আফ্রিকান লোককবিতার ছায়ায় তৈরি সেই গান। তাঁর মাথার কাছে এক বিরাট পূর্ণিমার চাঁদ! ‘খবর শোনাও, একটা খবর শোনাও, একটা ছোট্ট খবর তো শানাও ভাই…’। এভাবেই সমকালীন আধুনিক বাংলা গানের যে নবতরঙ্গ আমরা প্রত্যক্ষ করছিলাম ‘তোমাকে চাই’-এর সূত্রে, সেই আন্দোলনের শরিক এবং সমান্তর এক বিশিষ্ট সংগীতসাধক হয়ে ছোট ছোট বৈঠক, পথঘাট মেলা জটলায় গান শোনাচ্ছিলেন প্রতুলদা। মনে আছে, অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়া থেকে তাঁর কণ্ঠে ব্যঙ্গশাণিত উচ্চারণ ‘টুইডলডাম রাজা আরে ছি-ছি-ছি / এখন থেকে রাজা হবে টুইডল ডি’! আধুনিক কবিতা, আধুনিক গান, আধুনিক শিল্প যে একযোগে এক সচেতন সংস্কৃতিচর্চা, সেই নিরন্তর সন্ধানের প্রতীক ছিলেন প্রতুলদা। ‘রাজনৈতিক’ শব্দটিকে বহুমাত্রিকতায় উদ্ভাসিত করেছিলেন তিনি।
আরও পড়ুন-বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি মুছে ফেলতে নামবদল ঢাকা স্টেডিয়ামের
এখান থেকে স্বদেশ, স্বভূমি, স্বদেশবাসী আর নিপীড়িত মানুষের গানে ছিল তাঁর দায়বদ্ধতা। ‘দায়বদ্ধতা’। এতক্ষণে একটা জুৎসই শব্দ পেলাম, যার আপাদমস্তক জুড়ে আছে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গানের সঙ্গে। বহু আধুনিক, সমকালীন কবির কবিতায় তিনি সুর দিয়েছেন, বহু অনূদিত কবিতাকে ডেকে নিয়েছেন বাংলা গানের দাওয়ায়। ‘আমি যা কিছু মহান গ্রহণ করেছি বিনম্র শ্রদ্ধায় / মেশে তেরোনদী সাত সাগরের জল গঙ্গায় পদ্মায়…’। বাংলায় গান আর বাংলার গান গেয়ে রূপসী স্বদেশের করিমাকে অহংকার করে তুললেন তিনি। মনে পড়ছে, অরুন মিত্রের সেই বুক-কাঁপানো কবিতা ‘আমি এত বয়সে গাছকে বলছি…’, সুরে-সুরে দৃপ্ত ডানা মেলেছিল প্রতুলদার কণ্ঠে। ‘এক মাঠ ধান’—এই কথাকলিতে হঠাৎ একটা ছোট্ট টান দিয়ে বিস্তার দিতেন প্রতুলদা। মনে হত দূর-দূরান্ত জুড়ে একটা ক্ষেত, রক্তমাখা পা আর তাতে ভিজে ওঠা জীব যেন দেখা যাচ্ছে! অলৌকিক এক অভিজ্ঞতা।
দায়বদ্ধতা বললেই মনে হয়, প্রতুলদা জমজমাট তালিতে-তুড়িতে গেয়ে মাত করে দিচ্ছেন সেই গান—বোধহয় প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে ২০০৮ সালে, ‘আলু বে চো ছোলা বেচো / বেচো বাখরখানি / বেচো না বেচো না বন্ধু তোমার চোখের মণি…।’ তারপর সেই পঙক্তিতে কেঁপে ওঠা আমাদের—‘হাতের কলম জনমদুখী / তাকে বেচো না…।’ সুরেলা হামিং আর উঁচু পর্দায় সুরের সাতরংকে তিনি কথার ফাঁকে ফাঁকে বিস্ময়কর দক্ষতায় ঢুকিয়ে দিয়ে একটা কাণ্ড করতেন। চেনাশোনা গানের চেহারাটাই অন্যরকম হয়ে যেত। নিজস্ব এক ধারা, যার পূর্বসূরি বা উত্তরসূরি নেই। বেশিটা পশ্চিমা, কখনো কখনো পূর্বী সুরচলনের প্রবাহে-স্রোতে এক মিশ্রমাধ্যমের গান উপহার দিতেন তিনি।
কত কত মুহূর্ত, কত আন্দোলনের দমচাপা জমায়েতে, পুলিশের লাঠি আর রক্তচক্ষুর সামনে তাঁর গান ক্ষমতাহীনকে সাহস জুগিয়েছে। ২০০৭-২০১১ বিশেষত তাঁর গান ছিল আমাদের সঙ্গী। ‘এই তো যুক্তি জনগণের। এপথে মুক্তি জনগণের / অসিত শক্তি জনগণের / তুমি তো তাদেরই একজন / তুমি একাকী কখনও নও।’ – এ গান মুখে মুখে ফিরতো। তিনটে গানের কথা বলে, প্রতুলদার স্বাতন্দ্র্যকে চিহ্নিত করতে চাই। প্রথমটি কবীর সুমনের। ‘পেটকাটি চাঁদিয়াল…’। দ্বিতীয়টি অঞ্জন দত্তর। ‘নাম আমার আলিবাবা’। আর শেষে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের ‘ছোটো ছোটো দুটো পা / ছোটো দুই হাত’। তিনটি গানই শিশুশ্রমের ভারতবর্ষ নিয়ে। সবকটি গানই অতুলনীয়। আমার ব্যক্তিগতভাবে বুক মোচড়ায় যখন শুনি, প্রতুলদার উচ্চারণে—‘কুড় তাক্ তাক্ দাদা, কুড় তাক্ তাক্, / এক নয়, দুই নয়, দুশে দশ লাখ / দুশো দশ লাখ শিশু খাটে প্রাণপাত / ছোট ছোট দুটো পা ছোট দুই হাত।’
শেষবার জমিয়ে আড্ডা হল বছর তিনেক আগে। তিনি গেয়েছিলেন, যতদূর স্মৃতি যায়, ক্ষমতার নিশ্ছিদ্র মাতব্বরির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত একক আন্দোলনের গান, একটা প্রত্যয়, একাটা অঙ্গীকার—‘রাত যত হবে সঙ্গীন / ভোর ততই হবে রঙ্গিন…। সেলাম প্রতুলদা। মানুষের গান, আন্দোলনের গান, স্বপ্নের গান, রাস্তায়-ঘাটে-মাঠে ময়দানের গানে আপনি অক্ষয় দীপ্তিতে বিরাজ করবেন।
আরও পড়ুন-মিড-ডে মিলে সপ্তাহে ৩ দিন দেওয়া হবে ডিম
প্রতুলদার গাওয়া ক্যাসেট, সিডি, ব্যক্তিগত সংগ্রহ, তথ্যচিত্র—সবটা মিলিয়ে একটা সযত্ন সংরক্ষণ থাকা প্রয়োজন। এমন করেও যে গান তৈরি করা যায়, একা দাঁড়িয়ে মানুষের বুকে বুকে উদ্দীপনা জাগানো যায়—সে কথা ওই গান ছাড়া বিশ্বাস্যই হবে না! বাংলা গান, বালা সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা, মনে হল মরদেহ থেকে একটু দূরে দাঁড়ি চোখ মুছছে। আপনার রক্তপাতাকার সাথীরাও দাঁড়িয়ে আছেন একসঙ্গে।
পুনশ্চ : বিপ্লবী কবি বেরাবাঙ্গারাজুর একটি কবিতা (তর্জমা, শঙ্খ ঘোষ) ‘কী আমাদের জাত আর ধর্মই বা কী’ গান হিসেবে তৈরি করেছিলেন প্রতুলদা। জাতপাতের বিভেদ বা ধর্ম নয়, মানুষে মানুষে অনশ্চর মানবিক মৈত্রীর প্রত্যয় সেখানে। এই মুক্তচিন্তার গান আমাদের তরুণ প্রজন্ম যেন অবশ্যই শোনে!