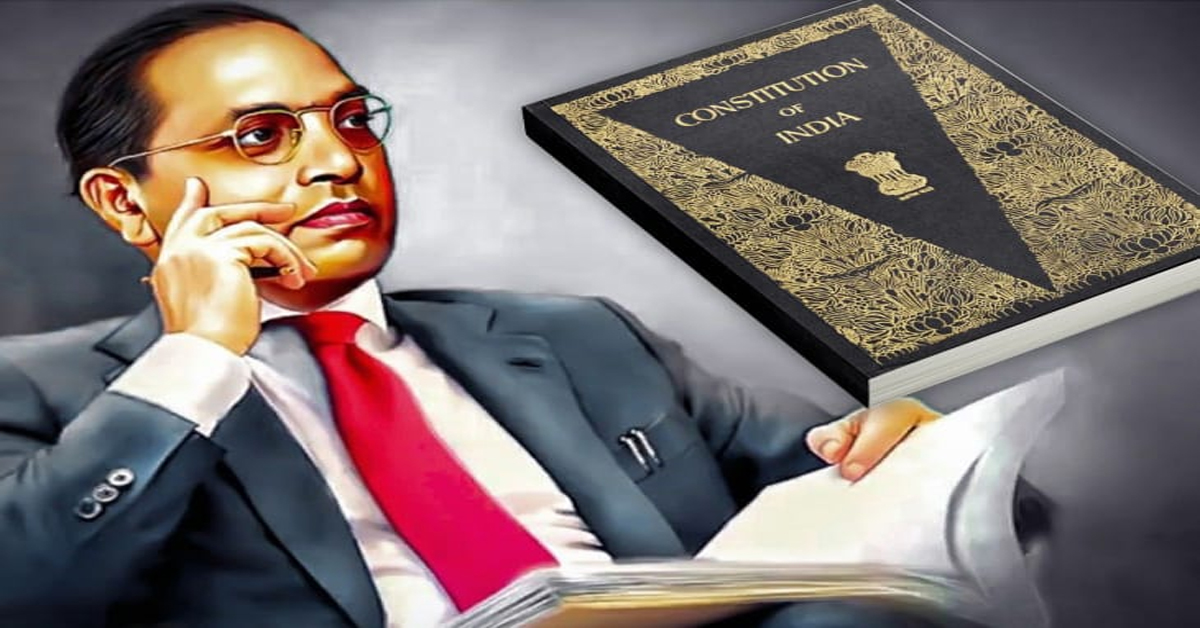ডক্টর বি আর আম্বেদকর (Babasaheb) সংবিধান রচনার সময় ভারতকে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ ও ‘সমাজতান্ত্রিক’ বলে ঘোষণা করার পক্ষপাতি ছিলেন না। ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব কি না তা নিয়ে মনে হয়ত তাঁর সংশয় ছিল। আর ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়টি বহুত্ববাদের ধারণার মধ্যেই অন্তঃস্থ ছিল। আলাদা করে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেননি। তবু ১৯৭৬-এ জরুরি অবস্থা চলাকালীন এই শব্দ দু’টি সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশে যোগ করে দেওয়াটা জরুরি মনে হয়েছিল কেন তা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে এবং হচ্ছে। শব্দ দু’টি সংবিধান থেকে বাদ দেবার জন্য সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলাও হয়েছে। শীর্ষ আদালত সেই সব মামলা খারিজ করেছে।
প্রশ্ন হল স্বাধীনতার ২৯ বছর পর সংবিধানের প্রস্তাবনায় ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ ও ‘সমাজতান্ত্রিক’ শব্দদু’টি যোগ করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল কেন? ধর্মের ভিত্তিতে মায়ের শরীর ছিঁড়ে পাকিস্তান জন্ম নিলেও ভারত-আত্মা কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার, সর্বধর্মসমন্বয়ের ধারণাতেই স্থিত ছিল। আর রেল, সড়ক, বিমান, জল-খাদ্য-সরবরাহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব অত্যাবশ্যকীয় সেবার দায়িত্ব তো কেন্দ্র আর রাজ্য সরকারগুলোর হাতে শুরু থেকেই ছিল। অর্থাৎ সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা না থাকলেও দেশ এগোচ্ছিল সমাজতান্ত্রিক চিন্তন অনুসরণ করেই। পরে কয়লা, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণও কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ধারণাকেই মজবুত করে। কিন্তু স্বাধীনতার আগে থেকেই পুঁজিবাদের, ধনতান্ত্রিকতার ঝোঁক এবং অশ্লীল চমকের ঝলক এ দেশে বরাবর ছিল। সেই প্রবণতা যে আরও বাড়বে এবং ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতা-শকটের চালকের আসনে বসে পড়বেন মুষ্টিমেয় ধনপতি এমন আশংকা করেই কি ব্যবস্থাপনাকে অন্তত খানিকটা সাংবিধানিক সমর্থন যোগাতে ‘সমাজতান্ত্রিক’ শব্দটা জুড়ে দেওয়া? লাভ অবশ্য কিছু হয়নি, ‘সমাজতান্ত্রিক’ ভারত আজ জিডিপির হিসেবে বিশ্বের পঞ্চম অর্থনীতি কিন্তু মাথাপিছু আয়ের হিসেবে তার স্থান ১৪৪, আর বিশ্ব-ক্ষুধা-সূচকে তার অবস্থান ১২৭ দেশের মধ্যে ১০৫-এ। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।
এই হল সংবিধান অনুসারে ‘সমাজতান্ত্রিক’ ভারতের অনাড়াল ধনতান্ত্রিক পটচিত্র। দূরদর্শী বাবাসাহেব সেই কবেই বুঝতে পেরেছিলেন কী হবে, কী হতে পারে।
আরও পড়ুন-খারাপ সময় চলছে! ‘কল্কি’র সিক্যুয়েল থেকে বাদ দীপিকা
আর ধর্মনিরপেক্ষতা? সংবিধানের ১৪ থেকে ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে ভেদাভেদ করা যাবে না। এ তো শুরু থেকেই ছিল। তবে? এখানেও সেই একই কথা। ১৯৭৬-এ এসে ভাবা হল নিয়ম আছে কিন্তু মানা হয় না, আর না-মানার প্রবণতা রাজনৈতিক কুস্বার্থ-সাধনে বেড়েই চলবে। ফলে প্রস্তাবনায় ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দটি জুড়ে দেওয়া হল। ফল কী হল? আজ দেশ যারা চালাচ্ছেন তাঁরা কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই আতংক ছড়াচ্ছেন ‘হিন্দু খাতরেমে হ্যায়’। মুশকিল হল ‘হিন্দু’ শব্দের অর্থই এখনও তর্কহীনভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। ‘হিন্দুত্ব’ কি কোনও ধর্ম না কি তা একটি ‘যাপন-পদ্ধতি’ মাত্র? দ্বিতীয় অর্থটি, বলা বাহুল্য, অধিক যুক্তিগ্রাহ্য। ফলে রাজনৈতিক পরিসরে ‘সনাতনী’ শব্দের অনুপ্রবেশ এবং বহুল ব্যবহার শুরু হয়েছে।
‘মন্দির হাম ওহি বানায়েঙ্গে’ হুংকার এবং উচ্চতম ন্যায়ালয়ের পর্যবেক্ষণ ‘হিন্দুরা বিশ্বাস করে ওইখানেই ভগবান রামের জন্ম হয়েছিল’ ফলে মহাকাব্যের নায়ক ঐতিহাসিক ‘ভগবান’ হয়ে গেলেন এবং ‘সনাতনীগণ’ লক্ষ-প্রদীপ জ্বালিয়ে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়িয়ে দিলেন।
এদিকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার মতো দায়িত্বশীল সাংবিধানিক পদে থেকেও এক ভদ্রলোক ক্রমাগত ‘মানুষের ভোট’ না চেয়ে কেবল ‘হিন্দু-ভোট’ চেয়ে বেড়াবেন কিন্তু সংবিধানের তাতে কোনও অবমাননা হচ্ছে বলে কেউ মনে করবেন না, এই হল ধর্মনিরপেক্ষতার বর্তমান ধারণা।
একদম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারি ধর্মের বজ্জাত-রাজনীতির ফাঁদ থেকে থেকে আমাদের সহসা নিষ্কৃতির পথ নেই। ক’দিন আগে এক পুরোনো বন্ধু ফোনালাপের সময় জানাল, সে শুনেছে তাদের জেলাটি নাকি মুসলমান বিশেষত রোহিঙ্গায় ছেয়ে যাচ্ছে। খোঁজ নিলে জানবেন অধিকাংশ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি সনাতনী কোনও ভিত্তি ছাড়াই এবং স্বচক্ষে একজনকেও দর্শন না করেও বিশ্বাস করতে ভালবাসেন যে তাদের এলাকায় গিজগিজ করছে সংখ্যালঘু, রোহিঙ্গা। জনগণনা, সরকারি রিপোর্ট বা নির্বাচক-তালিকার পরিসংখ্যান যাই বলুক উচ্চশিক্ষার কারণে তারা সে-সবে আস্থাশীল নন। বরং গোদি মিডিয়া আর হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়ানই তাদের সন্ত্রস্ত এবং সন্তুষ্ট করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। প্রসঙ্গত বিহারে এসআইআর করতে গিয়ে যে-সব ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাদের নাম-প্রকাশে নির্বাচন কমিশন বাধ্য হলে দেখা যায় তাদের একজনও বাংলাদেশ বা মায়ানমার বা অন্য কোনও বিদেশ থেকে আসা মানুষ নন। সর্বত্রই বিজেপি আইটি সেলের ছায়াবাজি এবং নির্লজ্জ গোদি-মিডিয়ার গোয়েবলসীয় বা গোবলীয় প্রচার।
আর এক বন্ধু জানালেন তাঁদের আবাসনে এক ব্যক্তি তার কাছে একটি আবেদন পত্র নিয়ে আসেন এবং বিচিত্র বাংলায় জানান প্রোমোটার কোম্পানি যাতে আবাসন-চত্বরে একটি ‘হিন্দু টেম্পল’ নির্মাণ করে দেন, এই দাবিতে তিনি গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন। বন্ধুটি সই করেননি, পরিবর্তে তিনি আবাসিকদের কল্যাণকামী সমিতির সদস্যকে ফোন করে জানতে চান মন্দির-মসজিদ বাদ দিয়ে আবাসিকদের জন্য একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আর অ্যাম্বুলেন্সের ভাবনা কি ভাবা যায়? তাতে উক্ত নেতা যিনি প্রথম সাক্ষাৎকারে নিজেকে বামপন্থী বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন, সহসা ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমার বন্ধু অযথা রাজনীতি করছেন। দেবাশীর্বাদ না থাকলে ডাক্তারে কী করবে? বন্ধুটি কি জানেন যে হিন্দুরা দিন দিন কীভাবে কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে? আবাসনের বাইরে বেরোলেই ওদের (পড়ুন মুসলমানদের) রবরবা। তিনি কি জানেন ইদের দিন অন-লাইন শপ থেকে গ্রোসারি আনাতে তার চার ঘণ্টা সময় লেগেছে। কারণ ডেলিভারি বয়েরা অধিকাংশই ওই? কেন হবে? তাদের এলাকাটি আবহমান কাল থেকে মূলত মুসলিম-অধ্যুষিত হলেই বা কী? যদিও বহুল-বহুতল গড়ে ওঠার পর নতুন চেহারায় এলাকাটির জনপরিসংখ্যানগত অবস্থান এখন একেবারেই অন্যরকম, সে-কথাও প্রমাণিত সত্য।
সত্যিই তো, সংখ্যালঘু ঘরের ছেলেরা অশিক্ষায়, দারিদ্র্যে ডুবে থাকবে, নিজের উৎসবের দিনেও ছুটি পাবে না, তারা সনাতনী-মুসলমান-খ্রিস্টান সর্বধর্ম-নির্বিশেষে যাবৎ মাফিয়া নেতার, রাজনীতি-ব্যবসায়ীর ঘুঁটি হয়ে পকেটে বোমা, হাতে পিস্তল বা ছুরি নিয়ে ঘুরবে আর আবাসিক সমিতির গণ্যমান্যগণ অনলাইন পিৎজা ভক্ষণ করে সন্ধ্যাবকাশে মন্দির-চাতালে মানসিক প্রশান্তির সন্ধানে আসনপিঁড়ি হয়ে বসবেন, ভবিষ্যতে এই হবে ধর্মনিরপেক্ষতার ছবি— বাবাসাহেব এ-কথাটিও মনে হয় সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে এই শব্দটিও তিনি সংবিধানের প্রস্তাবনায় লিখে রাখেননি।
আর সেই বিষয়টাকেই ঢাল করে বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসকশিবির সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের মতো ধারণাগুলোকেই ছেঁটে ফেলতে চাইছে।
নম্র কণ্ঠে কোনও উচ্চারণের পক্ষপাতী এঁরা নন, বোঝাই যাচ্ছে। তাই উচ্চকণ্ঠে সাংবিধানিক আদর্শ রক্ষার শপথ নিতেই হবে আমাদের।